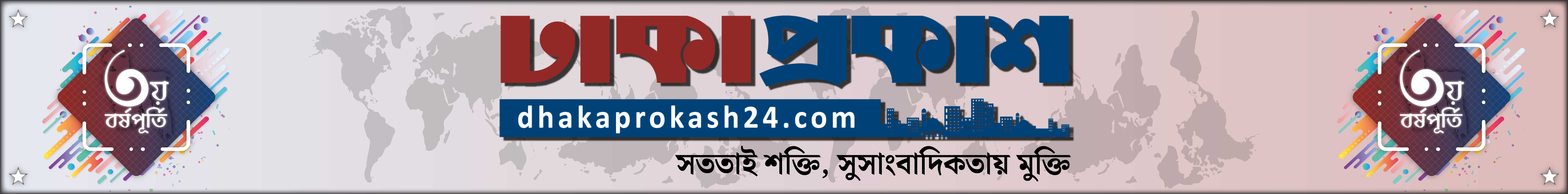সাক্ষাৎকারে আনু মুহাম্মদ (শেষ পর্ব)
নীতিনির্ধারণ করছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি বা বিভিন্ন থিংকট্যাঙ্ক

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সম্প্রতি ঢাকাপ্রকাশ’র সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছেন দেশের শিক্ষানীতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং করোনাকালের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শাহেরীন আরাফাত। আজ প্রকাশিত হলো সাক্ষাৎকারটির চতুর্থ পর্ব
ঢাকাপ্রকাশ: আমরা দেখছি যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি আছে। আমরা এটাও জানি, শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়টা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনি কী রকম দেখছেন? এ বিষয়টা একটু বিশ্লেষণ করে বললে ভালো হয়।
আনু মুহাম্মদ: অর্থনীতি মানে কী? শিক্ষার সঙ্গে তো সবকিছুই সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি এ রকম হয়–বিশাল সংখ্যক মানুষের কাজের, আশ্রয়ের কোনো নিশ্চয়তা নাই, তাহলে তাদের সন্তানরা শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যতটুকু প্রবেশ করার চেষ্টা করে, সেখানেও ঝরে পড়ার হার খুব বেশি থাকে। শ্রমজীবী মানুষের অনেক পরিবারে আমরা দেখি, তাদের খুব ইচ্ছা থাকে সন্তান লেখাপড়া করবে; কিন্তু একটা পর্যায়ের পর আর পারে না। প্রধান কারণ হচ্ছে–বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শিক্ষা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, রাষ্ট্র তা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। তার ফলে একটা বিরাট অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বঞ্চিত হওয়ার ফলাফল কী? ফলাফল হচ্ছে–তাদের মধ্যে যে সক্ষমতা ছিল, তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল, সেটা আর বাস্তবায়ন হয় না। তার ফলে আমরা যদি উৎপাদনশীল খাতের কথা চিন্তা করি, শিল্পের কথা চিন্তা করি, কিংবা অবকাঠামোর কথা চিন্তা করি–কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, নদী ব্যবস্থাপনা, বন ব্যবস্থাপনা–এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণ নাগরিকরা যে ভূমিকা রাখতে পারত, তা তারা পালন করতে পারছে না। সরকারের মুখে শুনি–আমরা তো সমুদ্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করতে পারব না, তাই বিদেশি কোম্পানি নিয়ে আসতে হবে। এই বিদেশি কোম্পানি আনার ফলে প্রকল্প অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যায়, অনেক বেশি অনিশ্চিত হয়ে যায় এবং এখন আমরা ক্রাইসিসটা দেখতে পাচ্ছি। এটা কেন হলো–বাংলাদেশের তরুণদের কি জেনেটিক্যালি কোনো সমস্যা আছে যে, তারা লেখাপড়া শিখতে পারবে না। তাদের সেই সুযোগটাই দেওয়া হয় না। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত চিন্তা থাকত যে, এসব বিষয় যে যেদিকে দরকার সেদিকে শিক্ষাগ্রহণ করবে, তাহলে অবস্থা ভিন্ন হতে পারত।
আমরা শুনি যে, বিশ্ববিদ্যালয় র্যাঙ্কিয়ে বাংলাদেশ অনেক পেছনে, গবেষণার র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ অনেক পেছনে। এসব ঘটনার প্রধান কারণ হলো–ওই পরিবেশটাই নাই। অর্থনীতি যেভাবে চলছে, তাদের দিক থেকে ওই চাহিদাই নাই। অর্থনীতি যদি চলে চোরাই টাকার উপরে, অর্থনীতির মধ্যে যারা ক্ষমতাবান তারা যদি বন দখল, নদী দখল, ব্যাংক দখল তারপর বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি, অনিয়ম সেগুলোর উপর ভর করেই চলতে থাকে এবং যদি দেখা যায় যারা ক্ষমতাবান তারা এ দেশের কোনোকিছু নিয়েই চিন্তা করে না, তারা মনে করে যে তারা বিদেশে থাকবে। এবং তাদের সন্তানেরা বিদেশে পড়াশোনা করবে। কী রকম একটা ভয়ংকর অসঙ্গতি যে, যারা দেশ পরিচালনা করছে, তারা দেশকে নিজের দেশ মনে করে না। নিজের বাসভূমি মনে করে না। আর যারা নিজেদের বাসভূমি মনে করে তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা নাই। সরকারি প্রাথমিক স্কুল যেগুলো আছে, সেখানে যদি সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী, এমপির ছেলে-মেয়েরা পড়ত; তাহলে তো প্রাথমিক স্কুলের এ অবস্থা হতো না। যদি তাদের সন্তানরা মাধ্যমিক স্কুলে পড়ত, এখানকার সরকারি কলেজে পড়ত, বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত; তাহলে তো এগুলোর এমন অবস্থা থাকত না। কিন্তু তারাই নীতিনির্ধারণ করছে। যারা নীতিনির্ধারণ করে, তাদের যদি নিজেদের একটা ওনারশিপ বা নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়; তাহলে তো ফল আসবে না। অথচ তাদের স্বার্থটা থাকে, সে কীভাবে আরও দ্রুত টাকা বানাবে কিংবা ক্ষমতার মধ্যে টিকে থাকবে, ব্যাংক থেকে টাকা আনবে এবং তাড়াতাড়ি কীভাবে বিদেশে সবাইকে সেটেল করবে–এই চিন্তাই তাদের থাকে; কিন্তু তারা তো নীতিনির্ধারণ করছে সব। তার ফলে অর্থনীতির যে প্রবণতা বা উন্নয়নের যে ধরন, সেই ধরনটার কারণে শিক্ষার যে প্রয়োজনীয় বিকাশের সম্ভাবনা, সেটা আর হয় না। কারণ নীতিনির্ধারক এবং সর্বজন–এ দুইয়ের মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি হয়। স্বাস্থ্যখাতেও তা-ই দেখা যায়। আজ বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালে যদি মন্ত্রী, এমপি, তাদের সন্তানরা চিকিৎসা করত, তাহলে তো পাবলিক হাসপাতালের এ দশা হয় না। তার মানে হচ্ছে–রাষ্ট্রের দায়িত্বে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সে প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈরি হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা।
অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করছে যেসব জায়গা, সেগুলোর সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নাই। যেমন–আমি অর্থনীতিতে, অর্থশাস্ত্রে আছি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থনীতি বিভাগগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের কোনো সম্পর্ক নাই। অর্থনীতির বিভিন্ন ধরনের নীতিনির্ধারক আছে, সেগুলোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথা। তাদের ইনভলভ করার কথা, সেগুলোর কোনো সম্পর্ক নাই। সেখানে নীতিনির্ধারণ কে করছে–নীতিনির্ধারণ করছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি বা বিভিন্ন থিংকট্যাঙ্ক। সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব থিংকট্যাঙ্ক, কিংবা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত থিংকট্যাঙ্ক–তারা নীতিনির্ধারণ করছে। তাহলে শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক কীভাবে হয়!
করোনার সময় ভ্যাকসিন–এগুলো তো কোনো ব্যাপারই ছিল না। বাংলাদেশে এতগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়–সেখানে ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা হবে, করোনা নিয়ে গবেষণা হবে–এসব নিয়ে গবেষণা করাই তো কাজ। সেগুলো নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। বন একের পর এক উজাড় করা হচ্ছে। বন কতটা দরকার–এগুলো তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন পাঠ্যসূচির মধ্যে থাকা দরকার।
আমি বলতে চাচ্ছি যে, বাংলাদেশের যে উন্নয়ন যাত্রা বা রাজনৈতিক ক্ষমতা–এ দুয়ের সম্মিলনে এমন একটা বিষবৃক্ষ তৈরি হয়েছে যে, সেখানে জ্ঞানের কোনো জায়গা নেই। জ্ঞানের কোনো প্রয়োজনই মনে করে না। তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয়, নিজেদের স্বার্থে কী দরকার। জনস্বার্থে কী দরকার, তার থেকে যোজন যোজন দূরে তো বটেই, তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েই অর্থনীতি এবং উন্নয়ন নির্ধারিত হয়। তার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাদের চরম উদাসীন না শুধু, বিরোধী একটা অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি।
ঢাকাপ্রকাশ: আমরা বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে এমন না, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার দরকারও নেই। একটা স্তর পার করার পর সে হয়তো নির্দিষ্ট একটা কাজে চলে যাচ্ছে, ওই কাজটা রাষ্ট্র বা সরকার তাকে দিচ্ছে। আমাদের দেশে ধারণাটা এ রকম হয়ে উঠেছে কি না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়লে চাকরি পাওয়া, বা এ রকম সুযোগ-সুবিধা সে পাবে না। আমরা দেখছি যে, পিয়নের চাকরির জন্য মাস্টার্স পাস ছেলে-মেয়েরা এপ্লাই করছে। শিক্ষার সঙ্গে কাজের যে সম্পর্ক, সে জায়গাগুলো আমাদের এখানে কীভাবে দেখা হচ্ছে?
আনু মুহাম্মদ: কর্মসংস্থানের বিষয়ে রাষ্ট্র এবং সরকারের অবস্থান হলো–কর্মসংস্থানের কোনো দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। এটা হলো সরকারের পজিশন–তোমরা নিজেরা কাজ খুঁজে নাও বা নিজেরা উদ্যোক্তা হও, ব্যবসায়ী হও। সুতরাং এটার সঙ্গে তো পড়াশোনার কোনো সম্পর্ক নাই। বরং দেখা যাচ্ছে–যাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নাই, তারাই দেখা যাচ্ছে যে, সরকারের বেশি কাছের। আসলেই যদি অর্থনীতির বিকাশের কথা আমরা চিন্তা করি বা জনস্বার্থের কথা চিন্তা করি তাহলে একটা পরিকল্পনার দরকার হয়। যেমন–এই খাতে কত ধরনের লোক দরকার, সেগুলো কীভাবে তৈরি হবে, সেটার জন্য একটা টাকা খরচ করতে হবে, সেটার জন্য দরকার মতো প্রশিক্ষণ দিতে হবে, দরকার মতো বিদেশ থেকে লোক আনতে হবে, বিভিন্ন দেশে লোক পাঠাতে হবে। এটা নিয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা থাকা দরকার। সে রকম কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা নাই, যে আমরা কোন খাতে, কী দরকার, সে অনুযায়ী কী ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার।
আমাদের দেশে কম্পিউটার, মোবাইল, গাড়ি যারা ঠিকঠাক করে; এরা সবাই দেখা যাবে যে, অনেক উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন–এদের কোনো ট্রেনিং নাই, নিজেরা নিজেরাই শিখে নিচ্ছে, বা আরেকজন ওস্তাদের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছে। একটা যে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া থাকবে, তা নেই। তার মানে বোঝা যায়–এরা যদি সুযোগ পেত, তাহলে অনেক ভালো টেকনিক্যাল কাজ করতে পারত। কিংবা তারা ইনোভেশন বা উদ্ভাবনের মধ্যে যেতে পারত। সেই সুযোগটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ব্যবস্থার মধ্যে নেই। যেমন–বাংলাদেশের সব গ্রামে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং কলেজ পর্যন্ত যদি রাষ্ট্রের দায়িত্বটা প্রধান থাকে, তাহলে সেখানে শিক্ষকের জন্যই তো অনেক কর্মসংস্থানের দরকার। এখন কোচিং সেন্টার যারা চালাচ্ছে, কিংবা টিউটোরিয়াল হোম চালাচ্ছে; তাদের তো কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম চালানোর দরকার নাই। তারা আরও সম্মানজনকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই শিক্ষকতা করতে পারত। প্রাইভেট, টিউশনি করে তার জীবিকা অর্জন করতে হতো না। এরাই তো এখন উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা। এখন মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করেও ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিংবা প্রাইভেট-টিউশনি করছে; নানারকম ধান্দা করতে হচ্ছে। কোথায় মামা, খালু আছে। কোথায় দশ লাখ টাকা দিতে হবে–এ সবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। মেধার চেয়ে তো এখন নিয়োগ বাণিজ্যটা প্রধান তৎপরতা। অর্থাৎ নিয়োগও এখন একটা অর্থনৈতিক তৎপরতা। কে কত টাকা দিতে পারে! মানে পুরো ব্যবস্থাটাই এমন এখানে সবকিছুই একটা কেনা-বেচার সম্পর্ক। যে কোনো জায়গায় টাকা-পয়সা দিলে আমি কাজ পাব–এই যে মানুষের একটা ধারণা, এর মাঝখানেই আবার বেশকিছু মধ্যস্তত্বভোগী তৈরি হয়েছে। তারপর টেকনিক্যাল দিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে, আমাদের আর্কিটেক্ট, আমাদের সোশ্যাল সাইয়েন্টিস্ট, সাইয়েন্টিস্ট, কম্পিউটার সাইয়েন্টিস্ট, আমাদের আইটি স্পেশ্যালিস্ট কী মাত্রায় দরকার, কী সংখ্যায় দরকার–সামনের ১০ বছরে, ৫০ বছরে, ১০০ বছরে সে অনুযায়ীই তো আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড় করাতে হবে। সেগুলোর কোনো পরিকল্পনা না থাকার ফলে প্রত্যেকটা একক ব্যক্তি, তার নিজের দায় থেকে কাজের খোঁজ করে। তার যদি কানেকশন থাকে, টাকা থাকে, সে যদি কোনো ধান্দা করে কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারে–এরকম করে সবাইকে একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে। সেটার পরিকল্পনার মধ্যে গেলে তো রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব নিতে হবে, রাষ্ট্র সে দায়িত্ব নিতে তো রাজি নয়।
এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রধান মনোযোগ হলো সরকারি কর্মকর্তা হওয়া, বিসিএস ক্যাডার হওয়া। তারা দেখতে পাচ্ছে বিসিএস হচ্ছে একমাত্র জায়গা–যেখানে স্থায়ী একটা কর্মসংস্থান, পাশাপাশি একটা ক্ষমতার ব্যাপার। আর এটা হচ্ছে একটা নিশ্চিত জায়গা। অন্য কোথাও নিশ্চয়তা নাই। সেজন্য তাদের মধ্যে একটা উন্মাদনা–সেই উন্মাদনার কারণে তাদের পক্ষে যে বিষয়ে মেধা আছে তাদের, যে যে বিষয়ে তারা ভূমিকা পালন করতে পারে; সেটাও করতে পারছে না। তাদের থার্ড ইয়ার থেকেই বিসিএসের বইপত্র মুখস্ত করতে হয়। বিসিএসে এমন ধরনের প্রশ্ন হয়–মুখস্ত করে সেখানে মেধা যাচাই করা হয়। তার ফলে শিক্ষার যে বিষ সেটা কর্মসংস্থানকেও প্রভাবিত করে। আর অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলের চেয়ে একটা লুণ্ঠনমূলক যে পরিস্থিতি এবং দেশের সামগ্রিক যে অর্থনৈতিক নীতিমালা, সেটা প্রণয়নে, বাস্তবায়নে দেশের যে বিদ্যায়তন, সেটার কোনো ভূমিকা না থাকার ফলে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
এসএ/
সাক্ষাৎকারে আনু মুহাম্মদ (পর্ব ১)
সাক্ষাৎকারে আনু মুহাম্মদ (পর্ব ২)
সাক্ষাৎকারে আনু মুহাম্মদ (পর্ব ৩)