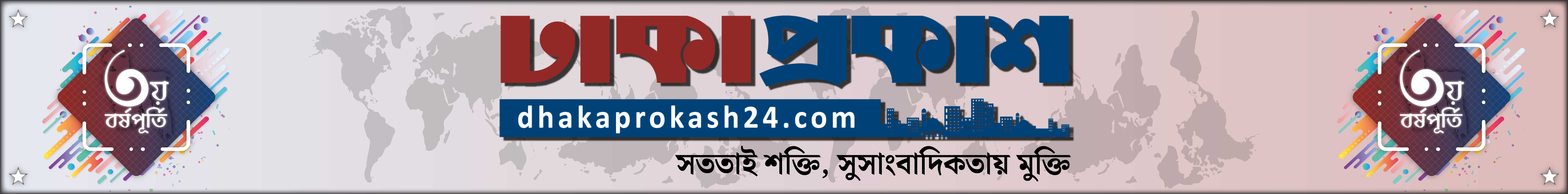সংলাপ: প্রত্যাশা এবং হতাশা

নির্বাচনপ্রিয় বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বেশি সংশয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে। জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন তো বটেই, এমনকি স্কুল-কলেজ পরিচালনা কমিটির নির্বাচনও এখন নির্বাচনী উত্তেজনার পরিবর্তে অবসাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয় গণঅভ্যুত্থান নয়তো নির্বাচন–এর বাইরে সরকার পরিবর্তনের আর কোনো পথ তো নেই। আর গণঅভ্যুত্থান তো নিয়মিত কোনো বিষয় নয়। তাই নিয়মিত নির্বাচনই সরকার পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি।
যদিও বলা হয় শান্তিপূর্ণ; কিন্তু নির্বাচনের আগে, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সেই শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য এবং অংশগ্রহণকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য নির্বাচন পরিচালনায় নিরপেক্ষতার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। সব নির্বাচন নিয়েই বিতর্ক আছে। তবে দল-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। তাই প্রত্যাশা ছিল সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন পদ্ধতি একটি স্থায়ী রূপ পাবে। তা হয়নি; বরং নির্বাচন নিয়ে স্থায়ী অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস, আস্থাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচনী ব্যবস্থার বিবর্ণ চেহারা দেখেছেন সকলেই। যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকেন, তারা সবাই সংবিধান মেনে চলেন, সংবিধানকে সবার উপরে স্থান দেন–এ কথা যত উচ্চস্বরে বলেন, নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠনের আইনের কথা উঠলে ততটাই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। অথচ নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন প্রণয়নের কথা সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।’
সংবিধানে এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও গত ৫০ বছরে কোনো সরকারই এ আইন প্রণয়ন করেননি। সবার শাসনামল গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগ বলতে কারো ক্লান্তি নেই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবাই নীরব। আইনের শাসনের কথা এত বলা হয়, অথচ সংবিধান উপেক্ষা করাও তো এক অর্থে আইনের শাসনের পরিপন্থী।
সংবিধানের দোহাই দেন যারা, রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন এবং ছিলেন সকলেই। বর্তমান সরকার তো বলছে, সংবিধানের বাইরে তারা পা ফেলতে পারবেন না; কিন্তু সংবিধানে আইন প্রণয়ন না করে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে কমিশনে নিয়োগ প্রদানের কোনো বিধান নেই। আবার সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সব কাজই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। তাই এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস তো থেকেই যায় যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটি (সার্চ কমিটি) প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের বাইরের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে না। ফলে অনুসন্ধান কমিটি এবং তার সুপারিশে গঠিত নির্বাচন কমিশন কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও বিতর্ক থেকেই যাবে। নিকট অতীত তার বড় তিক্ত দৃষ্টান্ত।
গত ৫০ বছরে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন না করার প্রধান কারণ হলো ক্ষমতাসীনদের কোনোরূপ বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ। একটি আইন প্রণীত হলে কিছু বিধিনিষেধ মেনে এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে কমিশনে নিয়োগ দিতে হতো। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোভাবে তাদের হাত-পা বাঁধা পড়ুক তা অতীতে তো বটেই বিগত ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লিগও চায়না, তাই তাঁরা সাংবিধানিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আইনটি প্রণয়ন করেননি।
গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নতুন ইসি গঠনে রাষ্ট্রপতি যে সংলাপ শুরু করেছেন, তা নিয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের তেমন কোনো আগ্রহ ও উৎসাহ নেই। দলগুলোর নীতিনির্ধারকরাও মনে করছেন, এ সংলাপে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা আইন প্রণয়ন নিয়ে ইতিবাচক আলাপের কোনো সম্ভাবনা নেই।
গত দুটো সংলাপের অভিজ্ঞতা বলছে, এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে সার্চ কমিটি করে গঠিত ইসি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তাই প্রত্যাশা করতেও দ্বিধা রাজনৈতিক মহলের। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যখন আহবান জানান তখন ক্ষীণ একটা প্রত্যাশা উঁকি দিতেও পারে, একটু আশা অনেকেই করতে পারেন–তিনি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ইসি গঠনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবেন।
তবে ব্যক্তিগত সদিচ্ছা বা উদ্যোগ খুব ভালো ফল দেয় না। তাই ইসি গঠনে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আইন প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রায় সকলেই। কারণ এ যাবতকালে গঠিত ১২টি নির্বাচন কমিশনের মধ্যে ২০১২ এবং ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সংলাপের পর গঠিত দুটি নির্বাচন কমিশনই ব্যাপকভাবে বিতর্কিত ও সমালোচিত হয়েছে। ফলে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে বারবার। কিন্তু তা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। যদি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হয় এবং নির্বাচনে জনগণের ন্যূনতম আস্থাও ফেরাতে হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন আইন প্রণয়ন করে সে আইন অনুযায়ী ইসি নিয়োগের বিকল্প নেই।
নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সব অংশের মানুষের প্রত্যাশা, নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্ব, এমন ব্যক্তিদের হাতে অর্পিত হওয়া উচিত, যারা তাদের অতীত কর্মকাণ্ডে যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যাদের উপর জনগণ ভরসা করতে পারে এই ভেবে যে, দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের সৎসাহস দেখাবেন। তিনি বা তারা নিজের এবং পদের মর্যাদা রক্ষা করবেন।
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির আলোচনা বা মতবিনিময় বা সংলাপ শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। ইতিমধ্যে সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি দেখা করে তাদের মতামত জানিয়েছে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলকে (জাসদ) সংলাপের জন্য ২২ ডিসেম্বর এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপি জোটের বাইরের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলকে (বাসদ) ২৬ ডিসেম্বর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিক যে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তাতে নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের বিষয়টিকে ‘মতবিনিময়’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শিগগিরই উত্তীর্ণ হচ্ছে, সেহেতু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন গঠনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।
একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক! বর্তমান নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের শেষ দিকে সংলাপ শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এক মাসের বেশি সময় ধরে সেই সংলাপ চলেছিল। তখন রাষ্ট্রপতি সব দলের কথা শুনেছেন, সৌজন্য দেখিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন গঠনে সরকারের বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো বা নাগরিক সমাজের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে আলোচনায় স্বস্তি থাকলেও ফলাফল হয়েছিল তার বিপরীত। এবারের উদ্যোগ সম্পর্কে অনেকেই বলছেন, বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সংলাপ বা মতবিনিময় কার্যত ‘আনুষ্ঠানিকতা’ ছাড়া আর কিছুই নয়। সংলাপের মাধ্যমে নতুন কিছু বেরিয়ে আসবে বলে তারাও মনে করেন না। কারণ অতীত তো তাদের জানা আছেই। এর আগে দুবার সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল। এবারও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটার সুযোগ নেই।
এ কথা ঠিক যে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা আছে। তবে তার প্রয়োগ নিয়ে সংশয় আছে। সাধারণভাবে এটাই মনে করা হয় যে, তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে কিছু করবেন না। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি সব দলের কাছেই শ্রদ্ধেয়। মতবিনিময় সভায় তার সদিচ্ছা থেকে তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কথা বলবেন, পরিবেশটাকে সহজ ও আন্তরিক করার জন্য রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা ঘটনার কথা বলে কিছুটা আনন্দঘন সময় অতিবাহিত করবেন, তার পক্ষ থেকে হয়তো নানা আশ্বাস দেওয়া হবে, রাজনৈতিক উত্তেজনাকে তিনি তার সৌজন্যমূলক ব্যবহারে শান্ত রাখার চেষ্টা করবেন। তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন গঠনে ক্ষমতাসীন দলের পছন্দই প্রাধান্য পাবে।
আগের দুই দফায় (২০১২ ও ২০১৭ সালে) মূলত আওয়ামী লীগের পছন্দ তাদের শরিক দলগুলোর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ফলে মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়েই নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে, এমন আলোচনা রাজনৈতিক অঙ্গনে রয়েছে। দুটি নির্বাচন কমিশনই (ইসি) তাদের কাজ এবং কথাবার্তার দ্বারা ব্যাপকভাবে বিতর্কিত ও সমালোচিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি একতরফা ও ভোটারবিহীন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনী সংস্কৃতিতে এক নতুন বিপর্যয় সৃষ্টি করে দেশ-বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। আর ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতি হয়েছে, এই ভোট দিনে না হয়ে আগের রাতেই হয়েছে বলে ক্ষমতার বাইরের সব মহল বলে আসছে। এরপর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক সমালোচিত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি।
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা হবে কিন্তু অনেকেই অংশ নেবেন না। তারা বলবেন এই আলোচনায় কোনো লাভ নেই, কেন তাহলে বৈধতা দেব? ক্ষমতাসীন দল বলবে আপনারা তো আলোচনাতেই এলেন না। তর্ক-পাল্টা তর্কে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও পরিবেশের উন্নয়ন হবে না। সামগ্রিক বিবেচনায় পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যাশাহীন তৎপরতা গতানুগতিকতার বাইরে কোনো ফল বয়ে আনবে না। ফলে গণতন্ত্র বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে নির্বাচন বিতর্কিত হওয়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হবে আরও।
লেখক: সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)
এসএ/