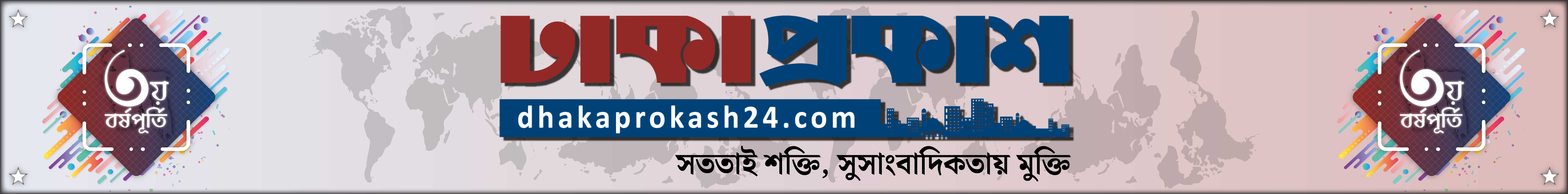চিরস্থায়ী সৃষ্টিসম্ভার রবীন্দ্রনাথ

যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা চিনি এবং জানি তিনি আমাদের বাঙালির অস্তিত্ব, তিনি আমাদের একান্ত নিজের মানুষ। আমাদের ভিতরের আমি যখন কথা বলি তখন আমরা তাঁর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত কৃতিত্ব যে তিনি আমাদেরই সব কথা একাই বলে গেছেন। একশ বছর পরের কথা বলে গেছেন অনায়াসে। আমরা যখন যা কিছুই ভাবি তা যেন রবীন্দ্রনাথের মত করেই ভাবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আমাদের চিন্তা-চেতনার সাংস্কৃতিক পরিধি বিস্তারের প্রতিটি স্তরে একটু একটু করে এগিয়ে দিয়েছেন। বাঙালির মনের বিকাশকে এই এগিয়ে দেবার যে ভূমিকা সেটাই তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ রূপে বিবেচিত হতে পারে। আলাদা করে তাঁর শিক্ষা ভাবনার স্বরূপ খোঁজার কিছু নেই। এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিস্তৃত মহাসমুদ্ররূপ রচনাসমগ্র রেখে গেছেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই হল বাঙালির মনন ও চৈতন্যের বিকাশের জন্য শিক্ষাচিন্তার স্মারক এবং বাহক।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিক্ষা সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা ভাবনার প্রয়োগ দেখতে পাই। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা নিয়ে তিনি সময়ে অসময়ে অনেক কথা বলেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের প্রকৃতির সহযোগে শিক্ষার প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন অতীতের সেই শিক্ষাব্যবস্থা আবারও ফিরে আসুক। তিনি বলেছেন ‘মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদিগের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়। যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা সয় ভারবাহি জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।’ আরো বলেছেন ‘মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।’
শিক্ষাকে তিনি কখনো অনায়াস অর্জনের বিষয় করে তোলেননি অর্থাত ‘জলো’ করে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন না। ছাত্ররা যাতে শক্ত বিষয় ভাঙতে পারে বড় বড় কথা বুঝতে পারে সেই ব্যবস্থা তিনি করতেন। তাই তাঁর ছাত্ররা দ্রুতচিন্তা করার মত ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। ছাত্র জীবনে শিথিলতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি ছাত্রদের কঠিন বই পড়াতে তিনি দ্বিধা করতেন না। একবার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রকে তিনি Ruskin এর বই পড়িয়েছেন।
তিনি শান্তিনিকেতনকে নিজের শিক্ষাচিন্তার আদর্শে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি ঠিক মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নিজস্ব শিক্ষাদর্শন ও ভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আশ্রম পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের কথা ভেবেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শান্তিনিকেতনে প্রবাসিরাও বিদ্যার্জনের জন্য এসেছে তখন তিনি ভেবে খুশি হলেন যে, শান্তিনিকেতন বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র গন্ডী ভেঙে বাইরের ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। একে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকেন্দ্র করে তুলতে চেয়েছেন যেখানে শিশুকাল থেকে ছাত্ররা একসাথে থেকে একটি জাতীয় আদর্শ চর্চা করতে পারবে, যেখানে শিক্ষাচর্চা হবে সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত।
কবির গান নিয়ে ছিল দুর্বলতা, আবেগ; ঠিক তেমনি ছিল আত্মবিশ্বাস। কী ভীষণ দৃঢ়তায় তিনি বলতে পারেন আমার গান বাঙালিকে গাইতেই হবে। কোথায় পান এই আত্মবিশ্বাস? উনবিংশ শতকের যে-পর্বে কবির আবির্ভাব তখন বাংলাগানের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। একদিকে প্রচলিত নাগরিক সমাজের টপ্পা, কবিগান, তরজা, আখড়াই, হাফ আখরাই, ঢপ কীর্তন প্রভৃতি আপেক্ষাকৃত স্থূল রুচির ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পরিচয়-বাহক গান বাজনা। আরেক দিকে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মআন্দোলনের পথিকৃত রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের উত্সাহ উদ্দীপনায় রচিত নানাধরনের ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত, আরেক দিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় হিন্দুমেলার উপযোগী উদ্দীপনামূলক জাতীয় সংগীত। বাংলা সংগীতের এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। গীতাঞ্জলি রচনার আগ পর্যন্ত ১৯১০ সালের আগে রচিত কবির সংগীতগুলিকে আমরা এই ত্রিভুজক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসা কবির অনন্যপ্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর সুর, বাণীছন্দ, তাল, অঙ্গ, প্রকাশ এ সবেরই গীতরূপ আলোচনা করা যেতে পারে অসাধারণ সব সংগীতরচনা (composition) হিসেবে। তাতে নানা বৈচিত্র্য, বহু বৈশিষ্ট্য, রূপ, রস, বর্ণ ও বিবিধ, পূজা, প্রেম, স্বদেশ, বৈষ্ণবভাবনা, ব্রহ্মভাবনা এ সবেরই প্রকাশ দেখি নানাসুরে, নানারাগে, নানাছন্দে, নানাতালে। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বকীয়তার স্বাক্ষর তাতে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও নান্দনিকতার প্রকাশ যে গানে তা কিন্তু গীতাঞ্জলি পরবর্তী যুগে। যখন থেকে তার সমাজ চেতনা, স্বদেশচেতনা এবং ঈশ্বরপ্রেম এসে মিলে গেছে মানুষ আর প্রকৃতিতে। তখন তার গান আর গান থাকে না। হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতার স্বরূপ। সেখানেই কবির বিশ্বলোক আর অন্তর্লোকের মিলন হয়। তিনি গেয়ে ওঠেন গান :
‘গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি\’
অবিনশ্বর প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর গান শুরু থেকেই আমাদের জীবনের উপলব্ধি, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাথী হয়েছে। বাঙালি তাঁর সকল সংকট, সংগ্রাম অতিক্রম করেছে তাঁর গান গলায় ধারণ করে। এ কথা তো সবারই জানা, কেবল গান কেন তাঁর কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ বাংলাদেশের বর্তমান প্রাসঙ্গিক সময়ে বহু চর্চিত, বহু আলোচিত রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক; এই কথা সহজেই মেনে নিতেই হয় যে তাঁকে বাদ নিয়ে কেউ সম্পূর্ণ রূপে বাঙালি হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের প্রকৃত বাঙালি হয়ে উঠতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতেই হবে। কোথায় নেই তিনি! বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের জাদুকরি হাতের স্পর্শ পড়েনি শুধুমাত্র মহাকাব্য ছাড়া। একথা অনস্বীকার্য বাঙালি হয়ে বাঙালিত্ব গ্রহণ করতে হলে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। জন্ম থেকে মৃত্যু, বিরহ থেকে আনন্দ, বিষাদ থেকে আত্মপ্রকাশ সব কিছুর ভেতরেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় হলেন তিনি; এমনকি বাঙালির আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভাবনা এবং এই উপমহাদেশে প্রথম সমবায় তথা কৃষি ব্যাংকের ভাবনা এবং ক্ষুদ্র ঋণের কথা তিনিই প্রথম ভেবেছেন। তিনি জমিদারি থেকে দূরে গিয়ে দরিদ্র কৃষকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভাবনা এবং তাদের মুক্তির কথা; কারণ অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া শুধু শিল্প আর সাহিত্য দিয়ে কখনো মানবজাতির মঙ্গল সম্ভব নয়; আর এখানেই তিনি অনন্য। তিনি জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে নতুন মাত্রা দান করেছেন, তা তুলনাহীন। তাকে ঘিরেই বাংলা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ভুবনে আধুনিকতার সূচনা হয়েছে। পরবর্তী কালে এই ধারার ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্য বিষয় বৈচিত্র্যে, জীবন জিজ্ঞাসায় ও মানবিকতায় বিশ্বস্ত হয়ে উঠে। তার কাছে আমাদের অনেক ঋণ। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা আজ সমৃদ্ধ। শুধু সাহিত্যে নয় সংগীতে এবং পরিণত বয়সে চিত্রকলায় বঙ্গীয় চিত্রধারার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তিনি যে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন, পরবর্তীতে তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আমাদের দেশে রবীন্দ্র চর্চার ইতিহাস আজকের মতো এত সহজ ও সুন্দর ছিল না; তিনি ছিলেন দেশ কাল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এক মহাবৃক্ষের মতো আশ্রয়দাতা।
এই অঞ্চলের বাঙালি সব আনন্দ বেদনায়, সংকটে ও স্বপ্নে রবীন্দ্র সংস্কৃতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই তাঁকে অবলম্বন করেছেন। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের মননে ও জীবনে নিত্যস্মরণীয় ও প্রাসঙ্গিক। তিনি যে বহুমাত্রিক জ্যেতির্ময় ছিলেন সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তা আত্মস্থ হয়েছে বাঙালির এক হৃদয়ে থেকে অন্য হৃদয়ে, এই আনন্দের ফল্গুধারা হাজার বছর ধরে বহমান হবে এবং প্রাণ পাবে। এই সে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, তিনি তাঁর সকল কীর্তি, সকল গৌরব নিয়ে বহু উচ্চের, বহু দূরের একজন হয়ে যাননি, তিনি ইচ্ছা করলে হতে পারতেন, কিন্তু তা সত্তে¡ও আশ্চর্যজনকভাবে সমগ্র জাতির হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন নিজের চির আসন। তাঁকে যেমন আমরা আপন জন ভাবি, তিনিও ঠিক তেমনিভাবে আমাদের আপন ভেবেছেন, এই আত্ময় বোধটা ছিল পারস্পরিক এবং জন্ম জন্মান্তরের। রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহুবার বৃহত বিশ্বের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করেছেন বাংলার মাটিতে পা রেখে, তাই তো বলেছিলেন মোর নাম- এই বলে খ্যাত হোক/ আমি তোমাদেরই লোক/ আর কিছু নয়/ এই হোক শেষ পরিচয়!
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপথিক হয়ে দূরে গেলেও হৃদয়ে সব সময় ধারণ করেছেন দেশের ছবি, দেশ মায়ের ছবি। তাইতো ভারতের রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াসে তার সমর্থন ছিল নিঃশর্ত। এমনকি দাসত্বের গ্লানি তাঁর চিন্তা বা অনুভূতিকে কখন সংকীর্ণ করেনি তিনি প্রাচ্য সভ্যতার, তথা ভারতীয় সভ্যতার শক্তিকে চিত্তে ধারণ করে তারপর দৃষ্টি দিয়েছেন প্রতীচ্যের শক্তি ও সামর্থ্যরে দিকে এ এক অনন্য সমন্বয় সাধন হয়েছে তাঁর জীবনে। সমাজের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য দিক ছিল না, যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি। বিশেষ করে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে তার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, এ বিষয়গুলো অল্প বয়স থেকেই তাঁর ভাবনায় ও চিন্তায় দৃশ্যমান হয়। তিনি শিক্ষাবিজ্ঞানী ছিলেন না কিন্তু শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা তাঁর বেড়ে ওঠা প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিস্তৃত। অতি শৈশব থেকেই তিনি এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বিষহ পরিণতি অনুভব করেছেন এবং ব্যক্তিজীবনে সেই পরিণাম কখনই বিস্মৃত হতে পারেননি। ফলে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর আজীবন ভাবনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শিক্ষা। তাঁর সেই ভাবনা শুধু গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বপ্নকে ফলপ্রসূ করে তুলতে চেয়েছেন। পৃথিবীর কোনো কবি, শিল্পী তাঁর কাব্য ও শিল্পচর্চাও পাশাপাশি শিক্ষা নিয়ে এমন বিপুল ভাবনা ও কর্মযজ্ঞের স্বাক্ষর রাখেননি। উপমহাদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায়ই শুধু নয়, তাবত পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর শিক্ষা-দর্শনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচিত্র রীতিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে অনুসরণ করা হলেও এই দুর্ভাগা দেশে তার কোনো মর্যাদা আজো হয়নি। এছাড়াও যে দুর্বিষহ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যর্থ শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন সেই ব্যবস্থা কৌশল পরিবর্তন করে শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-ভাবনা নিয়ে সুপ্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা ও লেখালেখি হলেও তাঁর আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। বরং যতই দিন যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ততই তাত্পর্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি বিজ্ঞানের প্রতি-ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বপরিচয়’ বইটি পাঠ করলে তা সহজে বোঝা যায়। তিনি বইটি উত্সর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ সেকালের সাধারণ মানুষের চিন্তার জগতকেও অভাবিতপূর্ব বিস্ময়ে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। পাশ্চাত্যের শিক্ষাজগতে ও চিন্তাজগতে সে আলোড়নের ছায়াপাত ঘটেছিল অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই, ইউরোপে একাধিকবার ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে। অন্যদিকে ইংরেজের উপনিবেশ ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক সংযোগ একেবারেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে তা হবার কথাও নয়। এই অনুভবকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন বিশ্বপরিচয়ের সেই ভূমিকাস্বরূপ নিবেদনে: “বড় অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতকার্য করে রাখছে। উপায়ে তার মধ্যে একটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লেখা রচনাদি পড়া। এ জন্য চাই মনের স্বাভাবিক কৌতূহল এবং বিভিন্ন বিষয় জানার ইচ্ছে। ক্লাসের পড়া হিসেবে যা পড়তে হয় তার প্রতি আকর্ষণের শক্তিটা প্রায়শ কম থাকে- এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তির আনন্দ হিসেবে যখন তার আবির্ভাব ঘটে, তখন আনন্দটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।” রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথাটিও বর্ণনা করেছেন বিশ্বপরিচয়ের বিভিন্ন লেখায়। অতএব রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও ভাবনায় বিষয় বৈচিত্র্যেও ব্যাপকতা সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি প্রথম ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পান তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের জন্য। সুতরাং তাঁর মতো এত আধুনিক মনস্ক একজন মানুষ; যিনি আজ থেকে শত বছর আগেই সমান দাবি নিয়ে সব বাঙালির মনের কথা একাই বিশেষ করে তাঁর গান ও কবিতায় উল্লেখ করেছেন। আমরা যখনই মানসিক দ্ব›েদ্ব ও টানাপোড়েনের মুখোমুখি হই তখনই তাঁর লেখা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাই তাকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করে; তার জীবন দর্শন, মূল্যবোধ ও মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ আর কোনো বাঙালির জীবনে ঘটবে বলে মনে হয় না। সুতরাং এ কথা সহজেই স্বীকার করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। বাঙালিকে মননশীল ও সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করতে তাঁর বিকল্প নেই; তাই বাঙালির জাতীয় জীবনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। তিনি তার সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সব শাখার মধ্য দিয়ে যুগযুগ ধরে বাঙালিকে আলোর দীপশিখা দান করে যাবেন এটাই কাম্য।
নারী স্বাধীনতা বা অধিকার যখন উনিশ শতকে এক কথায় অকল্পনীয়, তখন কবি নারীকে তুলে এনেছেন তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্রে। নারীকে উপস্থাপন করেছেন স্বাধীনচেতা ও সাহসী হিসেবে, যা আজও একই রকম ভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে যে বিষয়টি পরিবেশবিদ তথা সমগ্র মানবজাতির অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়, তা হল বৃক্ষচ্ছেদন ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই এটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই প্রকৃতিবাদী দর্শনচিন্তার প্রতিফলনও রেখে গিয়েছেন কাব্যে, গানে, সাহিত্যে, যার প্রাসঙ্গিকতা কখনওই অস্বীকার করা যায় না। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক এবং অবিচ্ছেদ্য। তাই তাঁর চিরস্থায়ী সৃষ্টিসম্ভার বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আর সে সবের গ্রহণযোগ্যতাকে নিশ্চিত করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। রবীন্দ্রনাথকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথে জাতির ভবিষ্যত কর্মপন্থা তৈরি করতে হবে। উত্সবে, আনন্দে বা মহাসঙ্কটে রবীন্দ্রনাথই অনুপ্রেরণা, আশ্রয়। তাঁকে ধারণ করতে পারলে নবীন প্রজন্ম সমৃদ্ধি লাভ করবে। আর তবেই আমরা জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকীর গণ্ডি ছাড়িয়ে দৈনন্দিন জীবনে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে নিতে পারব। কিছু প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে যেন আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলে? কয়েক বছর আগে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের বন্দিদের দিয়ে বাল্মিকী প্রতিভা নৃত্যনাট্য করিয়েছিলেন নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়? আশ্চর্যজনক ভাবে দাগি অপরাধীদের অনেককেই বদলে দিয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা? অলকানন্দার কথায়, ‘‘আমি যখন বাল্মিকী প্রতিভা করতে শুরু করেছি, ওটা কিন্তু আড়াই বছর আগে? ওটা করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে এই নাচের মধ্যে দিয়ে, ছন্দের মধ্যে দিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা পরিবর্তন ভিতর থেকে হচ্ছিল? সেটা হয়তো মানুষ ওদের শিল্পী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য? ওরা যে দোষ করেছে, তার জন্য ওরা শাস্তি পাচ্ছে? আবার যে ভাল কাজ করছে, তার স্বীকৃতিও পাচ্ছে? ওদের যেন ভাল হতে ইচ্ছে হল? আমার মনে হল ওরা যেন সবাই দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী হচ্ছে?” এটা অনস্বীকার্য যে সেদিন হতে শত বর্ষ পরে নয়, তারও আরও পঞ্চাশ বছর পরে বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় অতি মাত্রায় প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ? সেটা নিঃসন্দেহে একটা ইতিবাচক দিক?
ডিএসএস/