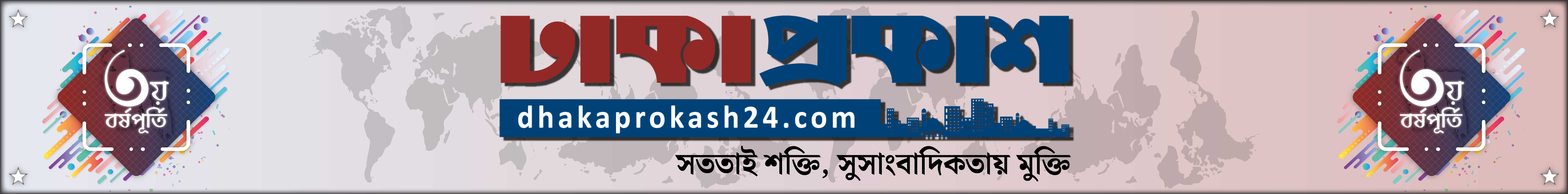ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এর মধ্যে সোমবার রাতেও দু’দেশের সেনাদের মধ্যে সীমান্তে গোলাগুলি হয়। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও কারাবন্দি নেতা ইমরান খানের মুক্তি দাবি করেছে প্রধান বিরোধী দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)।
পাকিস্তানি ইংরেজি দৈনিক দ্য ডন-এর বরাত দিয়ে মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) এমনটি জানানো হয়।
সোমবার সিনেটে পিটিআইর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ জাতীয় সংকটময় পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় সম্মেলন (Multi-Party Conference) আহ্বান করা প্রয়োজন, যাতে দেশের রাজনৈতিক নেতারা একসঙ্গে বসে জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই বৈঠকে ইমরান খানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তার জেল থেকে মুক্তিরও দাবি জানানো হয়।
পিটিআইয়ের সিনেটর আলী জাফর বলেন, “রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে এখন দেশের স্বার্থে ঐক্য প্রয়োজন। ইমরান খানের উপস্থিতি বিশ্বকে দেখাবে— পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ।” তিনি আরও বলেন, ইমরান যদি অংশ নেন, তাহলে তা হবে শক্তিশালী কূটনৈতিক বার্তা।
পিটিআই নেতা শিবলি ফারাজ আরও একধাপ এগিয়ে ইমরান খানকে টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তার দাবি, ইমরান টিভির মাধ্যমে জনগণকে মিনার-ই-পাকিস্তানে জমায়েত হওয়ার এবং ওয়াগা সীমান্তে পদযাত্রা করার ডাক দিলে এক কোটির বেশি মানুষ সাড়া দেবে।
তার ভাষায়, “শুধু জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি ভারতকে যথাযথ বার্তা দিতে পারেন।”
ক্ষমতাসীন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) বা পিএমএল-এন–এর সিনেটর ইরফানুল হক সিদ্দিকী ভারতের প্রতি কঠোর সমালোচনা করে বলেন, “পেহেলগামের হামলা আসলে একটি ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন— যা ভারতের নিজস্ব সংস্থারই পরিকল্পিত, পাকিস্তানকে হেয় করার উদ্দেশ্যে।”
তিনি বলেন, পাকিস্তান বরাবরই সন্ত্রাসবাদের শিকার, বরং ভারত এখন নাৎসি চিন্তাধারায় বিশ্বাসী সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করেছে। যদিও পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং বলছে, তারাই বরং দীর্ঘদিন ধরে চরমপন্থী হামলার শিকার। দুই দেশের মধ্যে এই উত্তেজনা বিশ্ব রাজনীতিতেও উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, পরিস্থিতি যুদ্ধাবস্থার দিকে গড়াতে পারে।