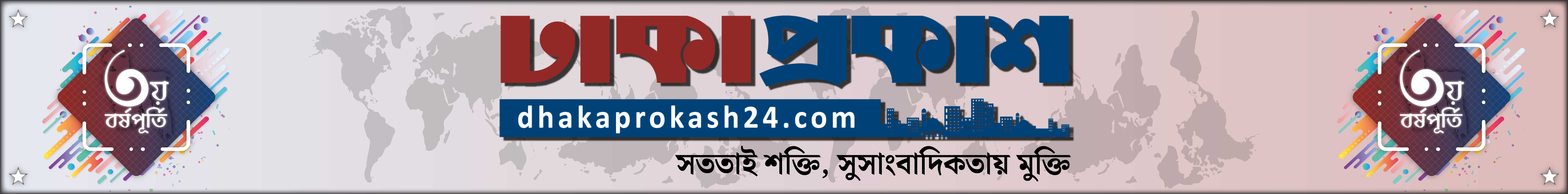আমি সরদার বলছি: সময় ও সমাজ

সরদার ফজলুল করিম [১৯২৫-২০১৪], সরদার নামে নিজের পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। এ কালের প্রজন্ম হয়তো তাঁকে সেভাবে জানে না। কারণ, বর্তমান বিশ্বে ও দেশে সরদারের মতো মানুষেরা প্রায় অবহেলিত বা অজ্ঞতার আড়ালে চলে যাচ্ছেন। সমাজের বাস্তবতা এমনই। স্মরণীয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কে অতিক্রম ও পালটানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং সমাজ গঠিত হয়েছে। এ অন্ধকার অতিক্রমণে যুদ্ধ করেছেন সরদার ফজলুল করিম ও তাঁর প্রজন্ম। এতে রয়েছে তাঁদের অসামান্য ত্যাগ ও আত্মদান। মূলত, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন বিকশিত হয়েছে।
উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ উপনিবেশে তাঁর জন্ম। ওই উপনিবেশাশ্রিত উদ্ভট ও তলানি-উৎস পাকিস্তানি উপনিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। আমাদের আলোচ্য আকরগ্রন্থ ‘আত্মকথা: আমি সরদার বলছি’[২০১৬/২০১৩]। এতে গ্রন্থিত হয়েছে বহুবিচিত্র ঘটনাবলি ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। অবশেষে তা আর ব্যক্তির স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এতে তিনি তাঁর সময়, সমাজ ও বাস্তবতার বিবিধ প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন। যা এ-কালের পাঠকসমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য-সূত্রে সামসময়িক অনেক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত আমরা গ্রহণ করতে পারি। কারণ এদেশের সামাজিক অনেক কারণ ও বৈশিষ্ট্য খুব একটা বদলায়নি। খোলস পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। যদিও উন্নত হচ্ছে ও এগিয়ে চলেছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা। আলোচ্য গ্রন্থের আলোকে তাঁর লেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও কতক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব।
(ক) সামষ্টিক বয়ান
(খ) ব্যক্তির উপলব্ধি ও সমাজবৈশিষ্ট্যের যোগসূত্র
(গ) প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার পটভূমি ও দ্বন্দ্ব
(ঘ) শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেষণা
(ঙ) সময় ও সমাজের ইতিহাস
(চ) সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ
(ছ) জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়।
একটি সংগ্রামের নাম সরদার ফজলুল করিম। অসম্ভব দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, আশাবাদে তিনি লড়াই করেছেন প্রগতিশীল ও সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এমন জীবন এখন কল্পনাই করা যায় না। যোগাযোগহীন, দারিদ্র্য, বৈষম্যপীড়িত, জীবন সম্পর্কে উদাসীন একটি সমাজব্যবস্থায় কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। সেখান থেকে ওঠে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিকল্প এক সত্তা হিসেবে। যে ব্যক্তির আচার আচরণ সমাজের অপর দশজনের সাথে মিলে না। তিনি মূলত সমাজবাদী। ফলে, প্রথাগত চালচিত্রকে অস্বীকার করেছেন। বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনার বাইরে নিবেদিত এক প্রাণপুরুষ। এ জন্য প্রচলিত কোনো ব্যক্তির উদাহরণ ও তুলনায় তাঁকে মূল্যায়ন করা যায় না।
বরিশালের পোলার ঢাকা জয়
কাল ও পরিবর্তনের ব্যবধানে বর্তমান ও চল্লিশদশকের ঢাকা শহর ভিন্ন ভূগোল। চল্লিশদশকের ঢাকা পর্যবেক্ষণে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সরদারের। বরিশাল-ঢাকার যোগাযোগ কেমন ছিল, তাও এ সময়ের প্রেক্ষিতে ভাবা যায় না। ফলে, যে-কোনো সচেতন ব্যক্তির ঢাকা আসা-যাওয়ার মধ্যে আবেগ ও বিস্ময় দুটো থাকাই স্বাভাবিক। তাঁর বর্ণনা থেকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। ১৯৪০ সালে মেট্রিক পাশ করে সরদারের ঢাকা শহরে আসার মধ্যে কত যে রোম্যান্টিকতা ছিল, তা কি আর বলতে হয়। বাদামতলি ঘাটে জাহাজ থেকে নেমে সেই বিস্ময়ভরা চোখে তিনি দেখেছেন ঢাকার রূপ ও চলাচল ব্যবস্থা। ‘‘ঝমঝম করে বিরাট জাহাজ( সেদিনকার সেই কিশোর এর চাইতে বড় জাহাজ যথার্থই দেখেনি) বরিশাল থেকে ছেড়ে বিরাট বিরাট নদীর বুকে ঢেউ তুলে, চাঁদপুর বন্দর এবং মুন্সিগঞ্জে নোঙর করে, নারায়ণগঞ্জের নদীতে ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার মীরকাদিম হয়ে সন্ধ্যার পরে যখন বুড়িগঙ্গায় ঢুকল, তখন কিশোরের চোখে পড়ল, দূরের রাস্তা দিয়ে আরো দ্রুতবেগে এক-চোখো কি একটা দৌড়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র কিশোরকে তার বিস্ময় আর ভয়ের ঘোর কাটিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয়ই বলেছিল: ‘ঐ দেখ রেলগাড়ি যায়।’’ [২০১৬: ১১৭]
এ বিষ্ময় কাটিয়ে ওঠে তিনি জড়িত হলেন সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রামে। পর্যবেক্ষণ করেছেন শুধু ঢাকা নয়, পূর্ববঙ্গের সমাজ ও জীবন। বিশ্লেষণ করেছেন মানুষের মনোজগত ও সামাজিক আচার আচরণ। তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি অনেক সামান্য বিষয়ও। উল্লেখযোগ্য যে, চল্লিশের দশকে আন্তঃসম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ, প্রণয় কল্পনা করা যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল ব্যবস্থাও ছিল সম্প্রদায়গতভাগে বিভক্ত। একই ভবনে হলেও আবাসন ব্যবস্থা ছিল আলাদা।
অনেক কাজের মাঝে সিনেমা দেখা ছিল তার নেশা ও ভালোলাগা। প্রতিটি সিনেমা দেখে নোট খাতায় সিনেমার নামও লিখে রাখতেন। ওই নোটবুক আবার ফিরে পেয়েছেন মধ্য বয়সে পৌঁছে। আত্মকথায় আনন্দের সাথে কয়েকটি নামও উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিপ্লবী ও লেখক সোমেন চন্দের মৃত্যু তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেয়। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ শ্রমিক মিছিলে নেতৃত্বে ছিলেন সোমেন চন্দ। ওই সময় প্রতিপক্ষের আক্রমণে তিনি নিহত হন। এ নির্মম হত্যাকাণ্ড সরদার মেনে নিতে পারেন নি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ভর্তি হয়েছেন। সোমেন চন্দের নিজের গড়া প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করেছেন একান্তই প্রাণের টানে। এ ছাড়াও সোমেন চন্দের সঙ্কেত গল্প নিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ ।
১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় তাঁর আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন। যদিও তাঁর আশেপাশে কারো জীবন এমন ছিল না। রাজনৈতিক হুলিয়া থাকার কারণে ওই সময় ঢাকায় থাকা নিরাপদ মনে করেনি তাঁর দল। এ জন্য দলের পরামর্শে তাঁকে কলকাতা যেতে হলো। কিন্তু সেখানেও গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা এড়ানো যায়নি। একদিন সত্যি তাঁকে পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে জানাচ্ছেন, তাঁর শারীরিক গঠন দেখে পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি তিনি সরদার ফজলুল করিম কি না। তারা মনে করেছে–এত ছোটখাটো ব্যক্তি সরদার ফজলুল করিম হতে পারে না। ‘‘পুলিশের লোকজন তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল, ‘নো’ ‘নো’ নট দিজ ওয়ান। সাম বিগ গাই। সাম বিগ সরদার ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল।’ এ কথাটাও আমার মনে আছে। ওরা আমাকে পছন্দ করছে না।’’ [২০১৬: ৬৩]
এ-ঘটনার পর তিনি চলে আসেন নিজের দেশে, তবে চলমান থাকে আন্ডারগ্রাউন্ড। দেশে ফিরে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন চালাকচরে। চালাকচরের লোকে জানতো তিনি আবদুল মজিদ বা বারুই সম্প্রদায়ের অশোক নামে। তবে সরদার ফজলুল করিমকে অনেকে না চিনলেও সাধারণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। কেউ কেউ তাঁর কাছেই জানতে চয়েছে–সরদার ফজলুল করিমকে চিনেন কি না। তিনি মনে মনে ভাবতেন–তবে উত্তর দিতেন না সরাসরি। কারণ নিরাপত্তার বিষয় জড়িত। আবার ‘মুসলমানদের মধ্যে কোনো কমিউনিস্ট নেতা আছে, এটা সে যুগে তাদের জন্যে একটা গর্বের ব্যাপার ছিল’। সরদারের লেখাতেই পাচ্ছি যে, কমিউনিস্টরা ছিল পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল। বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো চেতনা তখনও জাগ্রত হয়নি। এমন-কি সেকালের জাতীয়তাবাদী দলগুলোর মধ্যেও তা ছিল না। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের মুসলিম লিগ শাসকগোষ্ঠী বামপন্থি বা কমিউনিস্টদেরকে সবচেয়ে বেশি শত্রু মনে করতো। কারণ তারাই ছিল এগিয়ে থাকা অংশ, সচেতন ও সংবেদনশীল। এ ছাড়াও সমাজে এমনকি কারাগারেও জেলকর্মীরা বামপন্থিদের নিয়ে উপহাস করতো।
আমরা গল্প শুনতাম কারাগারে গেলে কারো কারো নবজন্ম হয়। বিশেষত রাজনৈতিক বন্দিরা লেখাপড়ার সুযোগ গ্রহণ করেন। কারাগারে পুলিশের তাড়া ও কর্মব্যস্ততা দুটোই নেই। সেই অখণ্ড অবসরের সময়টা কাজে লাগান বন্দিরা। সরদারের লেখায়ও এর উল্লেখ পেয়েছি। কারাগার জীবনের কথা বলতে বলতে একটি সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন। ‘জেলে অনেকেই লেখাপড়া ও গবেষণামূলক কাজ করতে পেরেছেন। সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অনিল মুখার্জী এঁরা সবাই জেলে বসে ভালো কাজ করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যেসব রাজবন্দি, তারা জেলখানায় গিয়ে চিন্তা করতেন, জেলখানার সময়টা তাঁরা কীভাবে ব্যবহার করবেন লেখাপড়ার কাজে। কিন্ত আমরা যারা মুসলমান রাজবন্দি আমাদের লেখাপড়ার কোনো ট্র্যাডিশন তেমন ছিল না। আমরা মুসলমানেরা জেলখানায় গিয়েই ভেঙে পড়তাম। আমাদের মধ্যে ভেঙে পড়ার যে প্রবণতা এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল।’ [২০১৬: ৭২] লক্ষণীয়, দেশভাগের পরও পূর্ববাংলার বিপ্লবী যারা ব্রিটিশ উপনিবেশের কারাগারে আটক ছিলেন তাঁদেরকে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দেয়নি। বরং এ তালিকা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে, ১৯৪৮ সাল থেকে আন্দোলনকারী রাজনীতিবিদদের প্রায়-স্থায়ী আবাস হয় জেলখানা। ব্রিটিশ শাসনের কারাগার সংস্কৃতি আরো বর্ধিত হয় পাকিস্তানের উপনিবেশে। নতুনভাবে জেলজীবন বরণ করতে হয়েছে এদেশের অসংখ্য কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের। এ বিষয়কে তিনি বিবেচনায় নিয়ে বলেছেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের কারাগারে যারা ছিলেন, তাদের নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার।
বস্তুত, পাকিস্তানের প্রতি অনেকেরই আবেগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পরপরই পূর্ববঙ্গে আন্দোলন জোরদার হয়। শুধু তাই নয় পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যারা সক্রিয় ছিলেন, তারাই আবার পাকিস্তানের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘পাকিস্তান নামক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রটি ছিল আমার বৈরিশক্তি। এই শক্তি আমাকে জেলখানায় আটকে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীটাকে তো আটক রাখতে পারেনি। এটা আমরা জেলখানায় বসেও বুঝতাম। পৃথিবী একটা গ্রহ, তার মধ্যে পাকিস্তান একটা উপগ্রহ, সেই উপগ্রহেরই আর একটা তস্য উপগ্রহ হচ্ছে জেলখানাটা।’ [২০১৬: ৯৭]
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সারাজীবন তিনি শিক্ষকতা করেছেন। এর ভেতরেও তিনি আন্দোলন সংগ্রাম থেকে সরে যাননি। বরং শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে কখনো বেছে নিয়েছেন রাজনৈতিক দায়িত্ব। পরিণামে কয়েকবার জেলযাপন। একসময় তাঁর কারাবন্দি জীবনই হয়ে ওঠে অনিবার্য। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, পাকিস্তানি শাসনামলে স্বাভাবিক জীবন তিনি যাপন করতে পারেননি। হয় কারাগারে থাকতে হয়েছে, না হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে। যে কারণে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিদর্শনের অনেককিছু কারো সঙ্গে মিলে না। এত অভিজ্ঞতা সাধারণ কোনো ব্যক্তির নেই। ফলে সরদারের চিন্তা, স্বতন্ত্র জীবনপ্রণালি একেবারেই ব্যতিক্রম। তাঁর মতো কেউ বাঁচতে চাইলে হতাশা আসাই স্বাভাবিক। এত দীর্ঘ নিপীড়নের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি কোনো প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে যেতেই পারেন। কারণ, সরদারের মতো ত্যাগী ও জীবনবাদী মানুষ এ সমাজে নগণ্য। তিনি প্রথাগত শিক্ষক ছিলেন না। তাঁর শিক্ষকতা, রাজনীতি, জীবনবোধ অতুলনীয়। আমরা যেসব জীবন পাঠ করি সাধারণ মনোবৃত্তির পরিসরে, এমন কাঠামোর বাইরে একজন সরদারের অধিষ্ঠান। জন্ম থেকেই ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের উপনিবেশ থেকে মুক্তির লক্ষে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। যেনো জাতিস্মর–প্রতিজ্ঞায় তাঁর লক্ষ নির্ধারণ এবং এ পথেই পরিক্রমণ। তাঁর জীবনপাঠে জ্ঞানচর্চা, এবং শ্রমিক, কৃষক শ্রেণির মুক্তির লক্ষে এক বিপ্লবী ও নিরন্তর জীবনযোদ্ধাকে আমরা পেয়ে থাকি। বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে ব্যক্তি-সুখের লোভনীয় প্রস্তাব প্রায়ই উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু জীবনার্থের ভিন্ন বিবেচনা, সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি দায়িত্ববোধ এসব থেকে তাঁকে বিরত রেখেছে। সামাজিক অসমতা, শোষণমুক্তির আন্দোলনে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে ছিলেন কমিটেড। এমনকি পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হয়ে তিনি আত্মপ্রতারণা করেননি। যেখানে প্রতারণার উদাহরণ সুলভ। অবশ্য নির্বাচিত এসব মেম্বাদের মধ্যে শ্রেণিগত একটা পরিচয় ছিল। এখান থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি; কেন পশ্চিম পাকিস্তান এদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার রুদ্ধ করেছে। সরদারের শ্রেণিবিশ্লেষণ থেকে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ‘কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মেম্বারদের মধ্যে একমাত্র আমিই বলতাম যে আমি কৃষকের ছেলে। আওয়ামী লীগের মেম্বারদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন এ্যাডভোকেট বা উকিল। ...পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা সবাই ছিলেন বড় বড় সামন্ত প্রভু।’ [২০১৬: ৯১-৯২]
লক্ষণীয়, তাঁকে কাছের অনেকে চিনতে না পারলেও শত্রুরা চিনেছে ঠিকই। পশ্চিম পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিষয়ে খুব সচেতন ও তৎপর ছিল। তাঁদের ভাষায় সরদার ফজলুল করিম ছিলেন ভয়ঙ্কর এক ব্যক্তি। উল্লেখ্য যে, তিনি কারাগারে থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও সরদারকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাঁর ভাষায় ‘‘ওয়াশিংটনে আমার নির্বাচনের খবরটা আসে এভাবে: ওয়ান কমিউনিস্ট ফ্রম জেইল ইলেক্টেড টু কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি।... আমেরিকান এ্যামবেসাডর ব্যাখ্যা দাবি করে করাচীতে পাকিস্তানের হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে। করাচীর হোম ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা দাবি করে ঢাকার আবু হোসেন সরকারের কাছে যে, ‘টেল আস, হাউ সরদার ফজলুল করিম হ্যাজ বিন রিলিজড!’ তখন আবু হোসেন সরকার কোনো রকম করে একটা কৈফিয়ত তৈরি করে জানান যে, সরদার ফজলুল করিমকে রিলিজ করা হয়নি।’ [২০১৬: ৯২]
তখন মিথ্যে অভিযোগে আবার তাঁকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়। সাম্রাজ্যবাদের চোখে সরদার ভয়ানক অপরাধীতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধা ও উদাহরণতুল্য একজন। দেশ স্বাধীন হলে ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করে। তার পর আবার তাঁর প্রিয় কর্মক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন আবদুর রাজ্জাক-এর আহ্বানে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এক কর্মচারী তাঁকে নিবিড় অবলোকন করেছেন। কর্মচারী ওসমানের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ‘সিগনিফিকেন্ট’ মনে করেছেন তিনি। স্বাধীনতার পর প্রথমদিন গ্রন্থাগারে দেখা হলে লাইব্রেরি-অ্যাসিসটেন্ট ওসমান তাঁকে বলেছেন, ‘‘স্যার আপনি তো একটা ডেঞ্জারাস লোক। আপনি সেই যে পাকিস্তান ভাঙবেন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লেন, পাকিস্তান না ভাইঙ্গা আপনি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরলেন না!’ আমার জীবনটাকে আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিনি। কিন্তু ওর অবজার্ভেশনটায় কিছুটা সত্য যে আছে তা অস্বীকার করি কি করে?’’[২০১৬: ১১০]
সামাজিক চালচিত্র
আমরা প্রায়ই শুনে থাকি ৫০-এর মন্বন্তর। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, মানে ১৯৪৩ সাল। এ-মন্বন্তর উপমহাদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে পরিবর্তন করে দেয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনবিচ্ছিন্নতার কারণে বিশেষত পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জনগণ দুর্ভিক্ষ, সংকট, মুদ্রাব্যবস্থা, বাণিজ্যের রকমফের, কূটনীতিবিদ্যা সম্পর্কে খুব একটা সচেতন ছিল না। তবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়েই মানুষের সচেতনতা তৈরি হয়, এবং বোধেরও পরিবর্তন ঘটে। সে কারণে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নতুন ধারণা ও সংবেদনার সৃষ্টি হয় বাস্তবতার অভিঘাতে। তখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ও স্বপ্নকে বিরত রেখে তিনি যোগ দেন মানবিক কাজে। বলেছেন, ‘‘এই দুর্ভিক্ষটা আমাদের প্রভাবিত করে। ...আমি তখন সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল–এ সমস্ত নিয়ে পড়াশোনা করছি। একদিন আমার কমরেড এসে বলছে, ‘তুমি কী এত লেখাপড়া করো? হেগেল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার মা-বোনেরা যেখানে মারা যাচ্ছে সেখানে তুমি হেগেল পড়ে কী করবে।’... সুতরাং আমি আমার হেগেলের কাছে থাকতে পারলাম না। পরদিন আমাকে যেতে হল নয়াবাজারে সিরাজদৌল্লা পার্কে।’’ [২০১৬: ৩৮-৩৯]
বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা লক্ষ করেছি। কী রাজনীতি, কী সাহিত্যচর্চা বা যে-কোনো সাধারণ বিষয়েও। তিনি যে কোনো বৈঠক, আলাপ, সিদ্ধান্তে স্পষ্ট কথা বলতেন। একবার বাংলা একাডেমিতে আমেরিকান দূতাবাসের এক সেক্রেটারি তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। এ প্রসঙ্গে সামান্য অংশ তিনি উপস্থান করেছেন। ‘‘ঐ সেক্রেটারি আমাকে বলে, ‘হোয়াই ডোন্ট ইয়ু জয়েন আস ইন লাঞ্চ?’ আমি তখন তাকে জবাব দিই, ‘ইয়োর টাইম ইজ ভ্যালুয়েবল এ্যান্ড মাই টাইম ইজ অলসো ভ্যালুয়েবল। লেট আস নট ওয়েইস্ট আওয়ার টাইম।’’ [২০১৬: ১০৩]
বস্তুত, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশভাগে অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষক দেশ ছেড়ে চলে যান। ওই সময় স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্ট পার্টির যারা সদস্য ছিল, তারাও চলে যায়। অর্থাৎ শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে তখন শূন্যতা তৈরি হয়। আবার মুসলমানদের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট পার্টি করতো, তাদের দিকে প্রশাসনের নজর বেড়ে যায়। কারণ এটা তাদের কাছে সহনীয় ছিল না। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান বাদ দিয়ে সরদার নিবিড়ভাবে যোগ দেন দলীয় কাজে। ‘মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ছেলে কমিউনিস্ট’ হওয়া, তখনকার সময়ে কঠিন কাজ ছিল। অন্যদিকে ডানপন্থার রাজনীতিতে সহিষ্ণুতা ছিল না। ফলে, ৪৫-৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বামপন্থি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল, তাদের ওপর মুসলিম লিগের সন্ত্রাসীবাহিনি আক্রমণ করতো। তখন মুসলিম লিগের ফ্যাসিস্ট গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হত্যাও করেছে। হলে হলে শিক্ষার্থীদের কক্ষ আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, ভাঙচুর করেছে। স্মরণীয়, ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নলিনী দাশ আন্দামান জেলে রাজবন্দি ছিলেন। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময়, তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁরই প্রতিবেশি লোকজন তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে। তখন তিনি হত্যা করতে আসা লোকজনকে বলেছেন, ‘আমাকে জবাই করে তোমাদের কি লাভ? এর চেয়ে আমাকে বরং পুলিশের কাছে দিয়ে দাও। তোমরা পুরস্কার পাবে।’ [২০১৬: ২৩] তাঁর লেখাতেই পাচ্ছি–ইন্টারমিডিয়েট কলেজে হিন্দু মুসলিম ছাত্ররা পাশাপাশি থাকলেও কখনো তাদের মধ্যে ঝগড়া, দাঙ্গা হয়নি। তবে আবাসিক ব্যবস্থা ছিল আলাদা। সংস্কারগত আচরণ ছিল বিভাজিত। এ থেকে সাম্প্রদায়িক বোধ ও চেতনা সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর মানসগঠনে অনেক শিক্ষকের ভূমিকা স্মরণ করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে স্মৃতিকথায় চমৎকার কিছু কথা লিখেছেন। তেমনই একজন পিসি চক্রবর্তী। বাস্তবতা হলো, তিনি ৪২-এর দাঙ্গায় নিহত হন।
সরদার নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চল্লিশ, পঞ্চাশ সালের পূর্ববঙ্গের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সরদার দেখেছেন, কোথাও মানুষের বিকাশ সমানভাবে হয়নি। ফলে সামাজিক বৈচিত্র্য নিয়েই গঠিত হয় রাষ্ট্র ও সমাজ। ব্রিটিশ উপনিবেশ বা এর আগে থেকে চলমান সম্প্রদায়গত আড়ষ্টতা, বা পিছিয়ে থাকার কারণে যে-হিংসার বিস্তার, এটিকে মুসলিম লিগপন্থিরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকে। ‘‘...মুসলমানরা একই ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের চাইতে ‘একেবারে ভিন্ন’ এরূপ ব্যাখ্যা-বক্তব্যের ওপর জোর দিতে থাকেন। যে ভারতীয় উপমহাদেশে, নানা ধর্ম, ভাষা ও জাতির অবস্থান, বিদেশি শক্তির থেকে স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে তার অপর কোন সমাধানের স্থানে মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র স্থাপন, তথা ভারত বিভাগের ওপরই এই নেতৃবৃন্দ তথা মুসলিম লীগ জোর দিতে লাগলেন। এখান থেকেই মুসলিম লীগের আন্দোলনটি ‘সাম্প্রদায়িক’।’’ [২০১৬: ১১৪] এমন পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। ফলত, ঢাকায় সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি, দল গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থান। একইসাথে মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও বামপন্থার আদর্শ বিকশিত হয়। যে–পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চল্লিশদশকের ঢাকা ও পূর্ববাংলাকে গুরুত্বসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সরদার কয়েকটি বিবেচনা তুলে ধরেছেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, এর ভিত্তি চল্লিশের দশক। ওই সময় আত্মবিকাশ ঘটে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির। সামগ্রিক বিকাশের বীজের অঙ্কুর ঘটেছে সে সময়। প্রগতিশীল ধারারও সূচনা হয় ওই দশকে।
দাঙ্গাবিষয়ক বিবরণ থেকে বোঝা যায়, সব ঘটনার একই ধরন ছিল না। তবে অনুমান করি, সমাজ ও মানুষেরা ছিল হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতায় নিমজ্জিত। না হলে এত খোলামেলা দাঙ্গা হওয়ার কথা নয়। এমনকি সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তাঁর ভাষায়, ‘আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই সে সময়ে, অর্থাৎ, ১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দাঙ্গা হয়। সেদিনকার দাঙ্গার কারণটা ছিল এ রকম: কার্জন হলে হিন্দু ছাত্ররা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছিল। সব ছেলেমেয়েরাই গেছে সেখানে, হিন্দু ছাত্ররা যেমন গেছে, মুসলমান ছাত্ররাও গেছে। বোধ হয় মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কেউ ইয়ার্কি করার জন্য কিছু ফুল বা পাতা বা এরকমের কিছু দোতলার ব্যালকনি থেকে হিন্দু মেয়েদের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ঐ এরিয়াটা ছিল হিন্দু ছেলেদের। পাশেই ঢাকা হল। হিন্দু ছেলেরা এতে অফেন্স নেয় এবং মুসলমান ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। [২০১৬: ৩৮]
তিনি ঢাকাকে ‘দাঙ্গার শহর’ বলে নির্ণয় করেছেন। কারণ দাঙ্গা বিষয়ে তিনি খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর আত্মকথা জুড়ে রয়েছে নানা ঘটনার সমাবেশ। এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ সময়ে এসেও আমরা লক্ষ করি। সরদারের বিবরণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়–এ-উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক অসুস্থতা আগে থেকেই ক্রিয়াশীল ও বিদ্যমান। এবং তা ভয়ঙ্করভাবে। এ-প্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, এর ‘শেষ কোথায়–কী আছে শেষে’। এ ছাড়াও ঢাকার দাঙ্গাকে তিনি অভিহিত করেছেন–‘ক্রনিক দাঙ্গা’ হিসেবে। এ ক্রনিক অসুখ থেকে এখনো মুক্ত হওয়া গেল না। তবে এর বিপরীতে গৌরবের বিষয়ও আছে। ‘৪৬-এ সাম্প্রদায়িক গণহত্যা হলো কলকাতাতে। তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতেও শুরু হয়ে যেতে পারত নরমেধযজ্ঞ। কিন্তু তা যে হলো না, সে স্মৃতি আমার সচেতন গৌরবের স্মৃতি।’ [২০১৬: ১৭৪]
সাধারণ মানুষকে চাপ প্রয়োগে ভাগ করা গেলেও তাদের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্য তখনো ছিল। তারা সবসময় মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করেছে। এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর বড়ভাই মঞ্জে আলি বামপন্থি বা কোনো রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না। ছিলেন সরকারি চাকুরে। রহমতপুরে সাবরেজিস্ট্রার থাকার সময় এক হিন্দু জমিদার পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়। এ-সুসম্পর্কের মধ্যে নিহিত আছে বাঙালিত্বের মৌল শক্তি। ‘‘আমার বড় ভাই মঞ্জে আলী তখন রহমতপুরে সাবরেজিস্ট্রার। সাবরেজিস্ট্রার একজন বড় অফিসার।... বড় ভাই একদিন সে বাড়িতে গেলে জমিদারের বৃদ্ধা স্ত্রী কেঁদে ফেলেন। বড় ভাইকে দেখে নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে যায়।... একদিন বড় ভাই আর আমি মাগরিবের নামাযের সময় গেছি সে বাড়িতে। সময়টা হিন্দুদের সন্ধ্যাহ্নিকেরও সময়। আমার বড় ভাই মহিলাকে বললেন, ‘মা, আপনার ধোয়া কাপড়টা দিন তো। কাপড়খানা বিছিয়ে আমি নামাযটা পড়ে নিই।’ একঘরে সন্ধ্যাহ্নিকের কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আর তার পাশের ঘরে বড় ভাই নামায পড়ছেন! আমি বলতে চাই, এটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা উপাদান, এই যে সমন্বয়–বন্ধুত্ব কিংবা আত্মীয়তা।’ [২০১৬: ৫৩-৫৪]
যে-বাঙালিত্বের সূত্রে পূর্ববাংলায় ঘটে গণআন্দোলন। একজন সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসেবে গণআন্দোলনের উত্থাল সময় তিনি অবলোকন করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ এখানে প্রযোজ্য বলে মনে করি। ‘১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন আমি নিজের চোখে দেখেছি।... ‘সত্যেন সেনের মতো একটা নিরীহ লোক একটা লাঠি হাতে কয়েদিদের সাথে মিছিল করে যাচ্ছে শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে, চিন্তা করুন একবার। এ ঘটনাটা আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ গণঅভ্যুত্থান।... ১৯৬৯-এ আগরতলা মামলা থেকে যে বঙ্গবন্ধু বের হলেন–এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তাকে দেখার জন্য আমি গেলাম তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে। আমি অবশ্য জানতাম যে জনতার ভিড়ে শেখ মুজিবের কাছে আমি যেতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি গেলাম, কারণ আমি মনে করতাম জনতাই হচ্ছে শেখ মুজিব এবং শেখ মুজিবই হচ্ছেন জনতা। এভাবে আমার একটা রাইট আপ আছে। রাইট আপটির শিরোনাম: তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।’ [২০১৬: ১০৩]
জীবনতৃষা
জীবন নিয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল ভিন্নতর। তিনি বলেছেন ‘জীবন জয়ী হবে’। আপাত রুদ্ধ করা গেলেও অবশেষে জীবনসংগ্রামের পরাজয় নেই। তিনি জীবনের জয়গান করেছেন অভিজ্ঞতা, ও লড়াইয়ের জ্ঞান থেকে। জীবনের প্রতি অসম্ভব নিবেদিত মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি আলাদাভাবে জন্মদিনের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতেন না। তাঁর ভাষায়,–‘আমি বলি, মানুষের মৃত্যুদিন হচ্ছে তার সত্যিকার জন্মদিন।’ ‘... কী দিতে পারি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে? আমি দিতে পারি আমার জীবনটাকে। শিশুকাল থেকে যেসব অসাধারণ মানুষ আমি দেখেছি তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি প্রজন্মকে।’ [২০১৬: ২০]
জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ভিন্ন বোধ আমাদের আশান্বিত করে তোলে। তা ছাড়া একটি ব্যতিক্রম ধারণার জন্ম দেয়। কথপোকথনের উত্তরে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখে বলেছেন, `Unless you enjoy your death you cannot enjoy your life.’ এবং তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি সর্বদা গোর্কীকে স্মরণে রাখি। জীবন কখনো মরে না। সময়হীন সময় ধরে জীবন অগ্রসর হচ্ছে। life is endless. মৃত্যুভাবনা নিয়ে কথা বলছি জীবনের আনন্দ উপভোগ অব্যাহত রাখার জন্য। একটা জীবন যখন মৃত্যুর হাত থেকে উঠে আসে সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমার সে অভিজ্ঞতা আছে। ... আমি ব্যক্তিগত মৃত্যুর প্রসঙ্গটিকে ব্যক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না। আমি কোন একলা মানুষ নই। আমার পরিবার, বন্ধুজন, পারিপার্শ্বিক, তোমরা সব মিলিয়ে আমি। আমি হচ্ছি সমাজের আমি।। আমি শুধু মানুষের সমাজের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি।’ [২০১৬: ৩১৯]
সেক্যুলারিজম প্রসঙ্গে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় স্পষ্টভাবে কথা বলেছেন তিনি। যেক্ষেত্রে কত ফাঁকি ও কৌশলী কত কথা বলেন অনেকে। এমন কায়দায় তিনি কিছু বলেননি। তাঁর বক্তব্য হলো: ‘উপমহাদেশজুড়ে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আর সেক্যুলাররা তাকিয়ে দেখছে। বক্তৃতা, মিছিল, মানববন্ধন করেই দায়িত্ব শেষ করছে। জীবন বাজি রেখে রুখে না দাঁড়ালে মৌলবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। ... আমি জানি না, সেক্যুলারিজমের বিকল্প কি হতে পারে। আমি এটুকু জানি যে, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কি করা যায় আমি জানি না। আমাদের সময়ে একটা সেন্টিমেন্ট ছিলো। একটা যৌথ সমাজ দাঁড় করাবার সেন্টিমেন্ট।’ [২০১৬: ৩১২]
তাঁর বিশ্বাস–জীবন কখনো মরো না। যদিও আমরা আপাত হাহাকার করি; হতাশায় নিমজ্জিত হই। অবশেষে সমাজ ও মানুষের সঙ্গে থাকাই জীবনের আনন্দ। সরদার ফজলুল করিম নিবেদিত ছিলেন মানুষের মুক্তির সংগ্রামে। ফলত, ‘আত্মকথা: আমি সরদার বলছি’ নিছক আত্মকথা নয়, সামষ্টিকতায় জীবন জয়ের ভাষ্য।
এসএ/